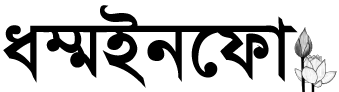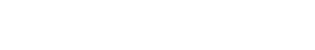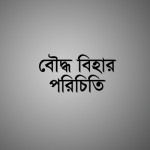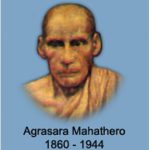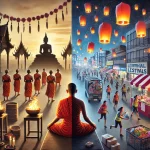খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে বিকাশিত বৌদ্ধ ধর্ম হলো বিশ্বের প্রাচীনতম ধর্মগুলোর অন্যতম। নেপালের কপিলাবস্তুতে খ্রিস্টপূর্ব ৫৬৩ অব্দে জন্ম লাভকারী গৌতমের দর্শন-চিন্তা থেকে বৌদ্ধ ধর্মমতের উৎপত্তি হয়েছে। বুদ্ধের শিক্ষা সৃষ্টির মতবাদ, আত্মার অবিনশ্বরতা, শেষদিনের বিচার, বিশ্বাস ইত্যাদি প্রচার করে না। বুদ্ধ দুঃখময় জগতের কথা বলেন, যা আমাদের অতি পরিচিত নিত্যদিনের জগৎ। বৌদ্ধ ধর্মকে অনেকে বলেন আধ্যাত্মিক পথ এবং প্রজ্ঞা ও নীতজ্ঞানের ওপর প্রতিষ্ঠিত একটি জীবন দর্শন।
বুদ্ধের মতে, জীবনের পরমার্থ এবং সর্বপ্রকার দুঃখ থেকে মুক্তির উপায় হলো জগতে নির্বাণ লাভ করা। বৌদ্ধ দর্শনের মূল বিষয় হলো মানব জীবনের ক্লেশ ও দুঃখসংক্রান্ত সমস্যার শিক্ষা। বুদ্ধ শিক্ষা দেন দুঃখ-কষ্ট লাঘবের উপায় হলো নির্বাণ অর্জন তথা দুঃখ সৃষ্টিকারী ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার বিনাশ সাধন। আটটি উপায়ে (অষ্টাঙ্গিকা মার্গ) নির্বাণ লাভ করা যায়। এগুলো হলো: সঠিক অনুধাবন, সৎ প্রতিজ্ঞা, সত্যবচন, সৎকর্ম, সৎজীবন, সঠিক প্রত্যয় বা প্রয়াস, সৎচিন্তা, একাগ্রচিত্ততা। আটটি পথকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। প্রথম দুটি প্রজ্ঞা, পরবর্তী তিনটি নৈতিকতা বা শীল এবং শেষ তিনটি হলো আরাধনা।
‘‘আমরা সত্যিসত্যি বুঝি না যে
সমস্ত কিছুর উদ্ভব আমাদের মন হইতে-
আর আমরা যাহা কিছু ভাবি না কেন
অচিরেই তাহা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে ছড়াইয়া পড়ে।’’ -গৌতম বুদ্ধ
বুদ্ধ মনে করতেন মানুষ তার চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেই সুখী হতে পারবে এবং তার মাধ্যমেই জগতের দুঃখ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারবে। তার এ ধারণাকে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারকরা ছড়িয়ে দিয়েছেন দুনিয়ার নানা প্রান্তে। বলা হয়, অন্তত দুটি কারণে বৌদ্ধ দর্শন বর্তমান বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমানায় অতীতকালে একটি স্বতন্ত্র স্থানের অধিকারী হয়ে উঠেছিল। প্রথমত, বাংলা হলো ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ধর্মের শেষ আশ্রয়স্থল, যেখানে তেরো শতকে মুসলিম আগমনের পরও বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রভাব টিকে ছিল। দ্বিতীয়ত, বাংলা হলো তান্ত্রিক বৌদ্ধ দর্শনের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র।
বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব কখন শুরু হয় এ বিষয়ে সুস্পষ্ট তথ্যের ঘাটতি রয়েছে। সম্রাট অশোকের (২৬৮-২৩২ খ্রিস্টপূর্ব) মিশনারি কার্যাবলি এবং বিদ্যবদান্ত ও অশোকবদান্তে সংরক্ষিত বুদ্ধ সম্পর্কে বিভিন্ন কাহিনী এবং ফাহিয়েন (৪০১-৪১০ খ্রি.), হিউয়েন সাঙ (৬৩০-৬৪৩ খ্রি.) প্রদত্ত তথ্যাদির আলোকে প্রতীয়মান হয়, সপ্তম শতকে বাংলায় বৌদ্ধ ধর্ম যথেষ্ট বিস্তৃত ও শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। বৌদ্ধ ধর্মের বিভিন্ন উপদল সম্পর্কে হিউয়েন সাং বলেছেন, পুণ্ড্রবর্ধনে হীনযান ও মহাযান উভয়ের কথাই উল্লেখ আছে।
সেই সঙ্গে অশোকের রাজত্ব এবং মৌর্য-পরবর্তী যুগের শিলালিপি ও অন্যান্য উৎস থেকে এটি সুস্পষ্ট হয়, অশোকের সময়ে বৌদ্ধধর্ম বাংলায় দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বগুড়া জেলার মহাস্থানে ব্রাহ্মী অক্ষরে একটি লেখা পাওয়া গেছে, যেখানে পুণ্ড্রনগরের কথা উল্লেখ আছে। সেখান থেকে খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ-তৃতীয় শতকে কিছু মৌর্য মুদ্রা ও অস্ত্রশস্ত্রও পাওয়া গেছে।
এসব কিছু থেকে অনেকে ধারণা করেন, এ গাঙ্গেয় বদ্বীপের কিছু অংশ তখন মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। চৈনিক পরিব্রাজক ইৎ সিং পশ্চিমবঙ্গের তাম্রলিপ্তি (তমলুক) ও কর্ণসুবর্ণের (বর্তমান বর্ধমান ও মুর্শিদাবাদ) নিকট এবং পুণ্ড্রবর্ধন (উত্তরবঙ্গ) ও সমতটে (বাংলাদেশ) অশোকের স্তূপ দেখেছিলেন বলে জানা যায়। এছাড়া মহাবংশ থেকে জানা যায় যে অশোকের রাজধানী পাটালিপুত্র থেকে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারকদের একটি দল এ বন্দর থেকেই শ্রীলংকায় সংঘ স্থাপনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিল।
পরবর্তী সময়ে মৌর্য রাজবংশের পতনের ফলে বৌদ্ধ ধর্ম রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা হারায়। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে পুষ্যমিত্র তার প্রভু বৃহদ্রথকে হত্যা করে মগধের সিংহাসন অধিকার করেন এবং শূঙ্গবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। শূঙ্গবংশের অভ্যুদয়ে বৌদ্ধ ধর্ম প্রথমবারের মতো কিছুটা বাধাগ্রস্ত হয়। তবে এ ধর্ম রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি।
পূর্ব ভারতীয় পণ্ডিতদের অভিমত ছিল, শূঙ্গরাজারা বৌদ্ধধর্মের প্রতি অসহিষ্ণু ছিলেন না এবং সে কারণে তাদের সময়ে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসারও ঘটেছিল। তাম্রলিপ্তিতে প্রাপ্ত একটি টেরাকোটা ফলক থেকে অনুমিত হয়, শূঙ্গরাজত্বে বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মের অস্তিত্ব ছিল। ওই ফলকটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে।
খ্রিস্টীয় প্রথম শতকে কুষাণরাজদের সময় বৌদ্ধ ধর্ম আবার নতুন করে শক্তি লাভ করে। রাজা কনিষ্ক বৌদ্ধ ধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্মে উন্নীত করেন এবং অশোকের মতো স্তূপ, চৈত্য ও বিহার নির্মাণ করেন। তিনি তিব্বতসহ বিভিন্ন দেশে ধর্মপ্রচারকদেরও প্রেরণ করেছিলেন। এ সময়ের প্রাপ্ত বিভিন্ন বুদ্ধমূর্তি, তাম্র ও স্বর্ণমুদ্রা এবং প্রত্নলিপি থেকেও কনিষ্কের আমলে বৌদ্ধ ধর্মের সমৃদ্ধি অর্জনের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।
বাংলার শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে বৌদ্ধ ধর্ম চর্চার প্রসার বেড়েছিল সমতটের দেব বংশ ও পাল বংশের শাসনামলে। বিচক্ষণ শাসক গোপাল ছিলেন প্রাচীন বাংলার বিখ্যাত পাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। গোপালের উত্তরসূরি ধর্মপাল, দেবপালও সাফল্যের সঙ্গে বৌদ্ধ দর্শনকে প্রচার করেছেন। বলা হয় পাল রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধ ধর্ম বাংলায় চূড়ান্ত বিকাশ লাভ করেছিল। কারণ পালরা ছিল বৌদ্ধ ধর্মের একনিষ্ঠ অনুসারী। তবে পাল রাজারা অন্যান্য ধর্মের প্রতিও সহনশীল ছিলেন। পাল রাজারা বেশকিছু বৌদ্ধ ধর্মচর্চা কেন্দ্র বা বিহার নির্মাণ করেছেন।
এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো উদন্তপুর, সোমপুর বিহার, বিক্রমশীলা, ট্রেইকুটাক, দেবিকোট, সংঘর, পতিকেরক, বিক্রমপুর ও জগদ্দল। তাই পাল যুগকে বাংলায় বৌদ্ধ ধর্ম প্রসারের স্বর্ণযুগ বলা হয়। কারণ এ সময়ে কেবল বাংলায়ই নয়, বৌদ্ধ ধর্ম তিব্বত ও মালয় উপদ্বীপজুড়েও বিস্তৃতি লাভ করে।
তবে পরবর্তী সেন রাজারা বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন না বিধায় তারা এ ধর্মে পৃষ্ঠপোষকতাও প্রদান করেননি।
বৌদ্ধ ধর্মের মূল দুটি সম্প্রদায় রয়েছে। হীনযান ও মহাযান। বুদ্ধের মৃত্যুর পর বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারীরা দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়। এই দুই ভাগই হীনযান ও মহাযান সম্প্রদায়। প্রথম সম্প্রদায় ব্যক্তি মনের নির্বাণ লাভকেই গুরুত্ব দিয়ে থাকে এবং দ্বিতীয় সম্প্রদায় মহাযান কেবল ব্যক্তি নির্বাণ নয় সমগ্র সমাজ নিয়েই তাদের চিন্তা-চেতনার প্রচার প্রসার করে।
পাল ও চন্দ্র শাসনামলে মহাযান সম্প্রদায় বজ্রযান ও তন্ত্রযান নামক দুটি দর্শনের বিকাশ ঘটিয়েছিল। এ সময়ে মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম তন্ত্র, মন্ত্র, মুদ্র, মণ্ডল, সাধন, নীতি পদ্ধতি এবং উপাসনার ওপর প্রতিষ্ঠিত তান্ত্রিক দর্শন দ্বারা ব্যাপকভাবে রূপান্তরিত হয়েছিল। নতুন এ ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের নেতারা বৌদ্ধ দর্শনে সিদ্ধ নামে পরিচিত। এরা সংখ্যায় চুরাশিজন ছিল বলে জানা যায়। বৌদ্ধ ধর্মের মরমিবাদী এ ধারার উৎপত্তি বাংলায় হয়েছিল।
এখান থেকে এটি ভারতের অন্যান্য অংশে বিস্তার লাভ করেছে বলে ধারণা করা হয়। সিদ্ধদের মধ্যে নেতৃত্বে ছিলেন: সারাহ্, নাগার্জুন, লুইপাদ, তিলোপাদ, লড়হপাদ, আদ্য বদ্র, কাহ্নপাদসহ প্রমুখ। বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র বিশেষ করে চর্যাগীতি সূত্রে জানা যায়, মরমিবাদী বৌদ্ধ ধর্মের তিনটি প্রধান শ্রেণী ছিল: বজ্রযান, সহজিয়া ও কালচক্রযান।
বজ্রায়ন ও সহজিয়া একই মরমি দর্শনের দুটি ধারাকে প্রতিনিধিত্ব করলেও দ্বিতীয়টিতে আনুষ্ঠানিকতার স্থান নেই বললেই চলে। বজ্রযানের মূল লক্ষ্যবস্তু হলো গুরু বা প্রভু। গুরু বজ্র বা শক্তির ধারক। তিনি সুউচ্চ চারিত্রিক পথের দিশারি। গুরুর পথ নির্দেশ ব্যতীত ধর্ম দর্শনের এ পথ অনুসরণ করা যায় না। সহজিয়া হলো বজ্রযান অনুশীলন বা সাধনার একটি মার্জিত রূপ, যেখানে ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা, আচারাদি বা মন্ত্রাদি এবং দেব-দেবীর পূজা-পার্বণের কোনো স্থান নেই। এ ধর্মমতের অনুসারীরা ঘর ছাড়া, তারা তাদের মহিলা সঙ্গীদের নিয়ে ভ্রাম্যমাণ জীবনে অভ্যন্ত থাকে। তারা মনে করে প্রত্যেক মানুষই বৌদ্ধত্ব অর্জন করতে পারে, তবে ধর্ম পুস্তক অধ্যয়ন করে নয়, বরং গুরুর শিক্ষা গ্রহণ করে।
তেরো শতকে বাংলায় মুসলিম শাসনের শুরুর পর পরই তান্ত্রিক দর্শন ও বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে সমন্বয় চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছিল। বৌদ্ধ ধর্মের যা কিছু স্বতন্ত্র ছিল তা চর্যাগীতির তান্ত্রিক রূপ। এটিও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সতেরো-উনিশ শতকের চৈতন্যোত্তর সাহিত্যে সহজিয়া বৈষ্ণববাদে রূপ নেয়। একসময়ের পরাক্রমশীল বৌদ্ধ ধর্ম বাংলায় তার প্রভাব হারিয়ে ফেলে। চৌদ্দ শতকে এর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হারানোর পরও বৌদ্ধ ধর্ম বেশকিছু জীবন্ত উপাদানে রূপান্তরিত হয়, যা কয়েক শতক ধরে বাংলার ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনকে অনুপ্রাণিত ও পরিচালিত করেছে। ভারতের অন্যান্য অংশে এর অবনতি বা বিপর্যয়ের পরও পূর্ব ভারতই একমাত্র অঞ্চল যেখানে তেরো-ষোলো শতক পর্যন্ত বৌদ্ধ ধর্ম শক্ত অবস্থানে টিকে ছিল।
বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস হাজার বছরের বেশি পুরনো। তাদের প্রথম দিককার ধর্মীয় স্থাপনাগুলো এখনো বাংলাদেশের প্রাচীনতম প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের গৌরব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা এখনো বাংলাদেশের প্রধান ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর অন্যতম। দর্শন, শিক্ষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ এ জনগোষ্ঠী মূলত বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রাচীন আরাকান সড়ক ধরে কক্সবাজার টেকনাফ পর্যন্ত ছড়িয়ে আছেন।